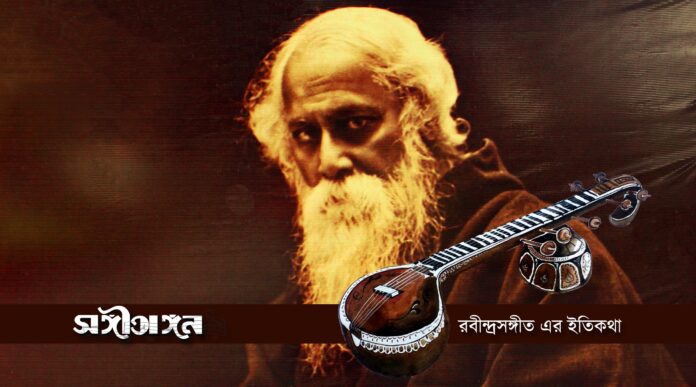– মোশারফ হোসেন মুন্না।
রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল জীবনের এক বিশেষ দিক। কবে তিনি প্রথম গান রচনা করেন, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কারও মতে ১২ বছর বয়সে তিনি প্রথম গান রচনা করেন; আবার কেউ কেউ বলেন, ১৮৭৫ সালে ১৪ বছর বয়সে তাঁর গান রচনার সূচনা। এ সময়ে তিনি অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সরোজিনী নাটকের জন্য ‘জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ’ গানটি রচনা করেন। সে বছরই হিন্দুমেলা উপলক্ষে দুটি গান ‘হিন্দুমেলার উপহার’ নামে ছাপা হয়। এর একটি ‘তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ’ রবীন্দ্র-রচনা হিসেবে অবিসংবাদিত; কিন্তু অপরটি ‘এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন’ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বা সুরারোপিত বলে অনেকে মনে করেন। জীবনের শেষ জন্মদিনের জন্য তিনি রচনা করেন ‘হে নূতন, দেখা দিক আমার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ’ গানটি। এটি রচিত হয়েছিল ২৩ বৈশাখ ১৩৪৮, অর্থাৎ ৬৮ বছর যাবৎ রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সংখ্যা ২২৩২ এবং সেগুলি অখন্ড গীতবিতান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা সঙ্গীতের ধারা ঠাকুর পরিবারে এসে একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্য রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গভীর ভক্তিরসাত্মক এক ধরনের সঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। এ বিষয়ে তাঁরা রামমোহন রায় এর অনুকরণ করেন। অগ্রজদের অনুসরণে ধ্রুপদ অঙ্গের ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করে রবীন্দ্রনাথ গানের এ ধারাটিকে সমৃদ্ধ করেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ধ্রুপদের প্রবল প্রভাব রয়েছে। নিয়মমাফিক ধ্রুপদ সঙ্গীতের চর্চা না করলেও পারিবারিক আবহের কারণে হিন্দুস্থানি ধ্রুপদের আদলে রবীন্দ্রনাথ অনেক ধ্রুপদ সঙ্গীত রচনা করেন।
ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব উপলক্ষে হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ ভেঙে তিনি বহু উপাসনা-সঙ্গীত রচনা করেন এবং এভাবেই তাঁর ধ্রুপদের পাঠগ্রহণ সম্পন্ন হয়। মূল ধ্রুপদের আদর্শে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি ধ্রুপদ ঐতিহ্যের নিদর্শন হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান। রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চার তুকের বহুল ব্যবহার এসেছে ধ্রুপদের অনুসরণে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বর, বাণী ও উচ্চারণে ধ্রুপদরীতির বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে বিষ্ণুপুর ঘরানার একাধিক ওস্তাদ ঠাকুরবাড়িতে শিক্ষাগুরু হিসেবে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী রবীন্দ্রনাথের মনের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেন। বাল্যকালে শোনা বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ছাঁয়া বিস্তার করে তাঁর সঙ্গীতের ওপর। রবীন্দ্রনাথ একই গানে বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ব্যবহার করে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন, যেমন ‘আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহ দহন লাগে’ গানটিতে তিনি পরপর চারটি রাগ ব্যবহার করেছেন। এ গানে ললিত, বিভাস, যোগিয়া এবং আশাবরী রাগের আভাস রয়েছে। ভাবের আকর্ষণে অনেক রবীন্দ্রসঙ্গীতেই এক রাগের ভিতর সেই রাগবহির্ভূত স্বর চলে এসেছে। এসব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মূলত রাগের অনুসারী নন, ভাবেরই অনুসারী। লোকসুরের গানেও রাগের মিশ্রণ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার শিল্পসাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। ‘দিনের পরে দিন যে গেল’ গানটির সঞ্চারী অংশে পরজ রাগিণীর স্বরগুচ্ছ এসে ‘পায়ের ধ্বনি’ গণনা করার আকুতিকে মূর্ত করে তোলে:
পায়ের ধ্বনি গণি গণি রাতের তারা জাগে,
উত্তরীয়ের হাওয়া এসে ফুলের বনে লাগে।
এভাবেই রাগ-রাগিণী ও লোকসুরের মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ একটি স্বকীয় ধারা তৈরি করেন।
সুরের দিক থেকে আর একটি অঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে, সেটি হলো টপ্পা। বাঙালির ভাবাবেগ প্রকাশে টপ্পার ব্যবহার সার্থক হয়েছে। ‘শোরি মিয়ার পাঞ্জাবি’ টপ্পার আদর্শে রবীন্দ্রনাথ কিছু গান রচনা করেন, যেমন: ‘এ পরবাসে রবে কে হায়’, ‘হূদয়বাসনা পূর্ণ হল আজি মম’, ‘কে বসিলে আজি’ ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর এসব গানেও টপ্পার অতি দ্রুত তান বা জমজমার ব্যবহার মূল গানের তুলনায় কম।
রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় টপ্পার গায়নে তালের সহযোগ দেখা যায় না। কাজ তথা টপ্পার দানাও কেবল আবেগের টানে কোথাও কোথাও যুক্ত হয়। তাল ছাড়া ঢালাগান ‘কখন দিলে পরায়ে’, ‘আমি রূপে তোমায় ভোলাব না’ ইত্যাদিতে উলিখিত প্রসঙ্গের সমর্থন পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-টপ্পাতে লোকসুরের ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। এরকম মিশ্রণের উদাহরণ: ‘তোমায় নতুন করে পাবো ব’লে’, ‘সকল জনম ভ’রে ও মোর দরদিয়া’ ইত্যাদি।
রবীন্দ্রনাথের যেসব গান তাল ছেড়ে ঢালাভাবে গাওয়া হয়, তার অনেকগুলি স্বরলিপিতে তালে বাঁধা আছে। এরকম গান ছাড়াও আজকাল আরও অনেক তালবদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত ঢালাগান হিসেবে গাওয়া হয়। বিখ্যাত ‘দারাদিম দারাদিম’ তেলেনা থেকে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট গান হলো ‘সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে’। এছাড়া শান্তিনিকেতন এর সেতারের শিক্ষক সুশীলকুমার ভঞ্জচৌধুরীর দুটি গৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব ছন্দোময় দুখানি গান রচনা করেন। তার একটি হলো ‘মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো’, অন্যটি ‘এসো শ্যামলসুন্দর’।
রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি বৈদিক ও বৌদ্ধ মন্ত্রে সুরারোপ করে মন্ত্রগান রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভান্ডারে মূল আদর্শের অনুসরণে কয়েকখানি দক্ষিণ ভারতীয় সুরের গানও আছে, যেমন: ‘বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী’, ‘বেদনা কী ভাষায় রে’, ‘শুভ্র প্রভাতে পূর্বগগনে উদিল’ ইত্যাদি। দক্ষিণ ভারতীয় সুরের প্রভাবে পরে আরও রচনা করেন ‘বাজে করুণ সুরে’ ইত্যাদি গান।
রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ-রাগিণীভিত্তিক ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি, তেলেনা ও টপ্পা ছাড়া অন্য যে সঙ্গীতের প্রভাব স্মরণীয়, তা হচ্ছে বাংলার লোকসঙ্গীত। রাগসঙ্গীতকে যদি বাংলাদেশের আকাশের সুর বলা হয়, তাহলে লোকসঙ্গীতকে বলা যায় এদেশের মাটির সুর। বস্তুত সব দেশের লোকসঙ্গীতেই থাকে সেদেশের মাটির সুর। বাউল, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত, সারি, এমনকি কথকতা থেকেও রবীন্দ্রনাথ সুর আর ভঙ্গি গ্রহণ করে তাঁর গানে দেশীয় সৌন্দর্য ও মাধুর্য সঞ্চার করেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর-অঙ্গের প্রসঙ্গে একথা গুরুত্বপূর্ণ।
কীর্তনের লোকসুর, শ্যামাসঙ্গীত ও রামপ্রসাদী সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ১৮৮৪-৮৬ সালের মধ্যে রচিত গানে। চুরাশি সালে কীর্তনের সুরে লেখা তাঁর প্রথম গান হচ্ছে ‘আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি’, পঁচাশি সালে শ্যামাসঙ্গীতের সুরে লেখা প্রথম গান ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্’ এবং ছিয়াশি সালে রামপ্রসাদী সুরে লেখা প্রথম গান ‘এবার ছেড়ে চলেছি মা’।
রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাউলের সুর পাওয়া যায় ১৯০৫ সাল থেকে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন যে, মাটির মানুষের সুর দিয়েই সর্বসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় সহজে। এই সময়ে লেখা কুড়িখানি গান নিয়ে বাউল নামে একটি বইও প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ছিল গান্ধীজীর প্রিয়গান ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে’। এটি একটি প্রচলিত লোকগীতি ‘হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে’ গানের আদর্শে রচিত। এই সময়কার লেখা ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি’ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। এই গানটিও কুষ্টিয়া অঞ্চলের বাউল গগন হরকরার ‘আমি কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে’ গানটির সুরে রচিত। বাউল সুরাশ্রিত আরও কয়েকটি বিখ্যাত গান হলো: ‘আজি বাংলাদেশের হূদয় হতে’, ‘তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে’, ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘আমি ভয় করব না’ ইত্যাদি।
‘এবার তোর মরা গাঙে’, ‘তোমার খোলা হাওয়া’ এসব গানে আছে সারিগানের সুর; আর কথকতার ধারা রয়েছে ‘কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি’ গানটিতে। কেবল বাংলাদেশের লোকগান নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের সুরও রবীন্দ্রসঙ্গীতে ব্যবহূত হয়েছে। যেমন, মুম্বাই প্রদেশের কানাড়ি গানের অনুসরণে ‘বড়ো আশা করে’ বা ‘সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে’ ইত্যাদি, গুজরাটি সুরে ‘কোথা আছ প্রভু’, মাদ্রাজি সুরে ‘এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ’, মহীশূরী সুরে ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’, শিখ ভজনের সুরে ‘বাজে বাজে রম্য বীণা বাজে’ ইত্যাদি গান রচিত।
পাশ্চাত্যদেশীয় গীতসুরের সঙ্গেও ঠাকুরবাড়ির পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে অল্পবয়সে আইরিশ মেলোডিস নামক একটি গ্রন্থের কথা রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি-তে আছে। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এক সময় পাশ্চাত্য সঙ্গীতের পাঠ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারেও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের চর্চা ছিল। সতেরো বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড যাত্রা এবং বিভিন্ন বিলেতি পরিবারে বসবাসের ফলে তাঁর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ধারণা আরও পুষ্ট হয়। এসব কারণে বাল্মীকি প্রতিভা (১৮৮১) এবং কালমৃগয়া (১৮৮২) গীতিনাট্যে বহু বিদেশী সুরের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের বেশ কয়েকটি গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন, যেমন: ‘ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে’, ‘সকলি ফুরালো স্বপনপ্রায়’, ‘কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া’, ‘আহা আজি এ বসন্তে’ ইত্যাদি।
রবীন্দ্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্য প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মূল গানের অনুসরণে কয়েকটি গান রচনা করা মাত্র নয়, ‘তোমার হল শুরু, আমার হল সারা’, ‘ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু’, ‘প্রাণ চায় চক্ষু না চায়’ ইত্যাদি গান পাশ্চাত্য রীতির চলন মনে করিয়ে দেয়। সাঙ্গীকরণের অসামান্য প্রতিভার দরুন রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বিচিত্র উপকরণ ব্যবহার করেও স্বতন্ত্র একটি রীতি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে শুধু সুর বাজলেও তাঁর গানকে রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে শনাক্ত করা যায়। কাজেই দেখা যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগ-রাগিণী, বাউল-কীর্তনের সুর, পাশ্চাত্য ঢঙের স্বরবিন্যাস সবই রবীন্দ্রনাথের আত্তীকৃত স্বকীয় সৃষ্টির নিদর্শন হয়ে উঠেছে।
সঙ্গীত প্রসঙ্গে সুরের পরেই আসে ছন্দ ও তালের কথা। চৌতাল, আড়া চৌতাল, ধামার, আড়াঠেকা, সুরফাঁক্তা, যৎ, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল, একতাল, তেওড়া ইত্যাদি তালে রবীন্দ্রনাথ গুরুগম্ভীর সঙ্গীত রচনা করেছেন। এছাড়া দাদরা, কাহারবা, আড়খেমটা তালেও অনেক গান রচিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এমন কয়েকটি তালে গান রচনা করেছেন, যেসব তাল উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতধারায় নতুন। এরকম তালের মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠী, ঝম্পক, রূপক্ড়া, নবতাল, একাদশী এবং নবপঞ্চতাল। পাঁচমাত্রার অর্ধঝাঁপ এবং দুই+দুই = চার মাত্রার কাহারবা তালেও রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে, তবে এই দুই তাল নতুন তাল হিসেবে গণ্য নয়। এর আগে উল্লেখিত ছয়টি তালই রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে।
এই ছয়টি তাল বিষমপদী, অর্থাৎ অসমান চলনবিশিষ্ট এবং এগুলিতে ফাঁক বা অনাঘাত নেই। যেমন, ষষ্ঠী তাল চলে দুই+চার অথবা চার+দুই ছন্দের ছয় মাত্রায়। দুই+চার ছন্দের গানের উদাহরণ ‘জ্বলেনি আলো অন্ধকারে’, ‘জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না’, ‘স্বপ্নে আমার মনে হল’ ইত্যাদি। চার+দুই ছন্দের গান ‘হূদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে’। ঝম্পক তালের চলন তিন+দুই = পাঁচ মাত্রার, দৃষ্টান্ত: ‘আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে’, ‘নিবিড় অমা তিমির হতে বাহির হল’, ‘আমারে যদি জাগালে আজি নাথ’ ইত্যাদি। রূপক্ড়া তালের মাত্রাবিভাজন তিন+দুই+তিন = আটমাত্রা। এই ছন্দের গান ‘জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে’, ‘শরত আলোর কমল বনে’, ‘গভীর রজনী নামিল হূদয়ে’ ইত্যাদি। নবতালে মোট নয়টি মাত্রা তিন+দুই+দুই+দুই হিসেবে চলে। এই তালের প্রসিদ্ধ গান ‘নিবিড় ঘন আধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা’। নবতালের নয় মাত্রার সঙ্গে আরও দুটি মাত্রা যোগ হয়ে এগারো মাত্রার একাদশী তাল হয়, যেমন: তিন+দুই+দুই+দুই+দুই ‘দুয়ারে দাও মোরে রাখিয়া’ এই তালের বিখ্যাত গান। পাঁচটি আঘাত আছে বলে আঠারো মাত্রার একটি নতুন তালকে নবপঞ্চতাল নাম দেওয়া হয়েছে। দুই+চার+চার+চার+চার মাত্রার সমন্বয়ে এই তালটি গঠিত। এ তালে কেবল ‘জননী তোমার করুণ চরণখানি’ গানটি রচিত হয়েছে।
নতুন তাল সৃষ্টি ছাড়া ছন্দের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রসঙ্গীতে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। চরণের বিভিন্ন পদের প্রথম শব্দটি ছেড়ে দ্বিতীয় শব্দের ওপর ঝোঁক দিয়ে চলনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে কিছু গানে, যেমন: ‘উতল ধারা বাদল ঝরে’ গানটি। রবীন্দ্রঙ্গীতে এই ছন্দোলীলা অবিরল।
একই গানে একাধিক লয় ব্যবহারের দৃষ্টান্তও আছে, যেমন: ‘এস এস বসন্ত ধরাতলে’। কখনও ধীর, কখনও দ্রুত ছন্দে গীত এই গানটি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ধীর-গম্ভীর উপলব্ধি প্রকাশে সার্থক। এক গানে একাধিক লয়ের দৃষ্টান্ত রয়েছে আরও কিছু গানে। যেমন ‘ওগো কিশোর আজি তোমার দ্বারে’ গানটি; এর প্রথমার্ধ মধ্যলয়ে গেয়ে শেষটুকু দ্রুতলয়ে গায়; সমগ্র গানটি তেওড়া তালে নিবদ্ধ।
একই গানে একাধিক তালবিন্যাসগুণেও রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষভাবে সমৃদ্ধ; এগুলিকে তালফেরতা গান বলা হয়। ‘নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ’ গানটিতে তাল-লয় উভয়েরই ভেদ আছে। প্রথমে মধ্যম লয়ে দাদরা তালের চলনের পর ষষ্ঠীর ছন্দে দ্রুতলয়ের গতিতে চলে আরম্ভের মধ্যলয়ে প্রত্যাবর্তন। তারপরেও আবার কাহারবা ছন্দের দ্রুতলয়ে সঞ্চরণ করে প্রারম্ভিক মধ্যলয়ে ফেরা। এরপরে গানটি ঝাঁপের দশমাত্রা ছন্দের দ্রুতচালে চলে আবার মধ্যলয়ে স্থায়ীতে ফিরে গিয়ে শেষ হয়। ‘ওই আসে ওই অতি ভৈরব হরষে’ গানটি কাহারবাতে শুরু হয়ে কিছুদূর চলার পর দাদরা ছন্দে কখনও ধীর কখনও দ্রুত চলতে চলতে ঐ তালেই সমাপ্ত হয়।
উদ্দীপনের গান হিসেবে ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’ একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই তালফেরতা গানটির প্রথম ছত্রটি কেবল চৌতালে বাঁধা। পরবর্তী ছত্র থেকেই তেওড়ার সাতমাত্রার চাল শুরু হয়; কিন্তু যতবার প্রথম ছত্রে ফেরা ততবারই চৌতাল ফিরে আসে। তারপর সব শেষের স্তবকটিতে ত্রিমাত্রিক বারো মাত্রার ছন্দে গতি দ্রুত হয়ে উঠে অন্তিমে আবার প্রথম ছত্রের ধীর চৌতালে গিয়ে মেশে।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংগ্রহকোষে ধীর লয়ের গান থেকে দ্রুতলয়ের গান পর্যন্ত সব রকম ছন্দের দেখা মেলে। সুধীর গতিতে রচিত ‘সুধাসাগর তীরে’, ‘জাগে নাথ জোছনারাতে’ বা ‘হেরি অহরহ তোমারি বিরহ’-র পাশাপাশি জলদ তালের ‘ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে’ বা ‘দেখা না দেখায় মেশা হে’ কিংবা ‘ওরে গৃহবাসী, খোল্ দ্বার খোল্’ ইত্যাদি গানের নমুনা অপ্রতুর নয়।
সঙ্গীতে সাধারণত সুর ও তালের প্রাধান্য থাকে বেশি, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতো কাব্যগীতি বা বাণী প্রধান গানে বাণীর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর বৈচিত্র্য বাঙালি জীবনের বিচিত্র ভাবগতিকে ধরে রেখেছে। তাঁর গানের প্রধান এবং শেষতম সংকলন গীতবিতানে গানের নানা পর্ব-বিভাগ রয়েছে। তাঁর ভক্তিমূলক গানগুলিকে ‘পূজা’ শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এরপরে আসে প্রেম ও প্রেমবৈচিত্র্যের গানের কথা। রবীন্দ্রনাথের ঋতুসঙ্গীতগুলি সাজানো হয়েছে ‘প্রকৃতি’ নামে। আরও আছে স্বদেশপ্রেমের গান, উদ্দীপনের গান, আনুষ্ঠানিক গান ইত্যাদি। বিষয়গুলিকে পূজা-প্রেম-প্রকৃতি-স্বদেশ-আনুষ্ঠানিক-বিচিত্র ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নাটকসূত্রে রচিত গানে কৌতুকজনক বিষয়ও পাওয়া যায়, যেমন: চিরকুমার সভা নাটকের ‘অভয় দাও তো বলি আমার wish কী’ বা ‘কাঁটাবনবিহারিণী সুর-কানাদেবী’, ‘আমরা না-গান-গাওয়ার দল রে’, ‘পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে’ অথবা তাসের দেশ নাটকের ‘হাঁচ্ছোঃ!, ভয় কী দেখাচ্ছ’ বা ‘চিঁড়েতন, হর্তন, ইস্কাবন/ অতি সনাতন ছন্দে/ করতেছে নর্তন’ ইত্যাদি গান।
পূজা, প্রেম ও প্রকৃতি বিষয়ক গানের বিভাজন নিয়ে অনেক সময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি আমাদের সারাক্ষণ ঘিরে রাখে বলে আমাদের পূজা-প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতি স্বভাবত যুক্ত হয়ে যায়। তাই পূজার গানে যেমন আসে প্রকৃতির প্রসঙ্গ, তেমনি প্রকৃতির প্রসঙ্গেও আসে পূজার কথা, যেমন: পূজা পর্যায়ের গান ‘শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে’, ‘আজি বহিছে বসন্ত পবন’, ‘আজি মর্মরধ্বনি কেন জাগিল রে’; প্রকৃতি পর্যায়ের গান ‘আমারে যদি জাগালে আজি নাথ’, ‘আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে’, ‘আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল’ ইত্যাদি। অনেক প্রেমের গানের সঙ্গে প্রকৃতি আর প্রকৃতির গানের সঙ্গে প্রেমও মিশে থাকে, যেমন: প্রেম পর্যায়ের গান ‘সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে’, ‘আজি এ নিরালা কুঞ্জে’, ‘চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে’ ইত্যাদি।
প্রকৃতি পর্যায়ের গানে প্রেমের প্রসঙ্গও যেন রবীন্দ্রনাথের নিকট দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। ‘আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে’, ‘এসো গো, জ্বেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি’ ইত্যাদি বর্ষার গান এর দৃষ্টান্ত। বসন্তের ‘মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে’ কিংবা ‘আজি শরততপনে’ গানগুলিতেও প্রেমের সংবেদন রয়েছে। এছাড়া প্রেম আর পূজার গানেও এরকম দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়, যেমন: প্রেম পর্যায়ের ‘সময় কারো যে নাই’, ‘আমার যদিই বেলা যায় গো বয়ে’, ‘আর নাই রে বেলা’ ইত্যাদি গান। পক্ষান্তরে পূজা পর্যায়ের ‘আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলেম গান’-এ প্রেমের ভাবই অধিক বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘বৈষ্ণব কবিতা’র উক্তি স্মরণ করা যায়: ‘যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা’। উপলব্ধির গহনে মানবমনের ভাবগুলি আপন সীমা ছাড়িয়ে পরস্পর সন্নিহিত হয় বলেই হয়তো গন্ডি টেনে বিষয় বিভাগ করা দুষ্কর।
রবীন্দ্রনাথের আনুষ্ঠানিক গানের বিষয়বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। বিবাহ, জন্ম-মৃত্যু, গৃহপ্রবেশ, বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, নলকূপ স্থাপন, রাখিবন্ধন, সমাবর্তন, অনুষ্ঠান উদ্বোধন, ফসল-কাটা, এমনকি মেয়েদের যুযুৎসু শিক্ষা (সঙ্কোচের বিহবলতা) উপলক্ষেও তিনি গান লিখেছেন। ফলে, বাঙালির সুখে-শোকে-কর্মে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে উঠেছে অপরিহার্য।
রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীর পদবন্ধও অসাধারণ। ধ্রুপদের ধরনে চার তুক ব্যবহারেই শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীবিন্যাস নিবদ্ধ নয়। তাঁর প্রথম যুগের রচনা ‘শাওন গগনে ঘোর ঘনঘটা’ গানটির গঠন ভিন্ন রকমের। স্থায়ী অংশটুকু গেয়ে একবার মুখে ফেরার পরে বাকি অংশ একটানা শেষ হয় বলে সঞ্চারী আর আভোগ অংশ নেই। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের বাইশ বছর বয়সে লেখা ‘আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে’ গানটি শুরু হয়ে আর প্রথম চরণে ফেরে না; সতেরোটি ছত্র সুরে সুরে অগ্রসর হয়ে একেবারে শেষ ছত্রে গিয়ে থামে।
দীর্ঘপদের অনেক গানেই চার তুকের হিসাবে মিলবে না, যেমন: ‘যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে’, কিংবা ‘ওগো কিশোর, আজি তোমার দ্বারে পরান মম জাগে’ অথবা ‘এই তো ভালো লেগেছিল’। পদবন্ধে বিশিষ্ট গদ্যগানও আছে রবীন্দ্রনাথের, যেমন: ‘অসুন্দরের পরম বেদনায় সুন্দরের আহবান’ বা ‘ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন’ ইত্যাদি।
খেয়ালের ধরনে কেবল স্থায়ী আর অন্তরা এই দুই তুকের গানও আছে রবীন্দ্র-রচনায়, যেমন: ‘সখী, আঁধারে একেলা ঘরে’, ‘তুমি কিছু দিয়ে যাও’, ‘নিশিদিন মোর পরানে’ ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের মতে কবিতার যেখানে শেষ, গানের সেখানে শুরু। তাঁর বক্তব্য এই যে, বাণীর ব্যঞ্জনার চেয়ে সুরের ব্যঞ্জনা অধিক দূরপ্রসারী। কথায় নিহিত স্পন্দনকে বিস্তৃত করার জন্য তিনি পরম আনন্দে সুরের পাখা মেলতেন; অনেক কবিতাকে সুরের ইন্দ্রজালে ঘিরে গীতশিল্পের নব রূপায়ণ ঘটাতেন তিনি; যেমন চিত্রা কাব্যের ‘উর্বশী’ কবিতার গীতরূপ ‘নহ মাতা, নহ কন্যা’ কিংবা বলাকা কাব্যের ‘ছবি’ কবিতার গীতরূপান্তর ‘তুমি কি কেবলই ছবি’।
শেষজীবনে গীতবিতানের ভূমিকার ‘প্রথম যুগের উদয় দিগঙ্গনে/ প্রথম দিনের ঊষা নেমে এল যবে’ কবিতাতেও সুরারোপ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী এ পর্যন্ত ৬৩ খন্ড স্বরবিতানে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি আকারমাত্রিক স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেছে। আরও কিছু স্বরলিপি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। বস্তুত কাব্যগীতিতে বাণী, সুর, ছন্দ ও তালের ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বাণীসম্পদ ভাবানুযায়ী সুরছন্দে বাহিত হয়ে সন্ধান করে অধরা মাধুরীর।